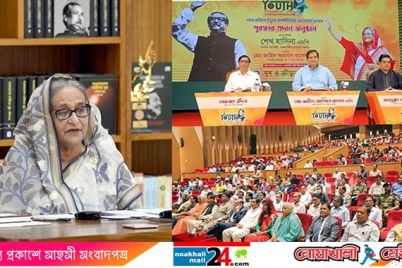মিরাজ মৃত্তিক ।।
মানুষের জীবনে সবছেয়ে অসহায় অবস্থা হলো পরিবার কারো অসুস্থতার সময়টা। আমাদের সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা নাই বললেই চলে। সরকারী হাসপাতালে গেলে রেশিরভাগ দায়িত্বরত ডাক্তর বলেন, আপনার যে সমস্যা এর এখানে কোন চিকিৎসা হবে না। আপনি বরং অমুক ক্লিনিক বা হাসপাতালে যান। আমিও সেখানে বসি বিকালে ভালো টিকিৎসা পাবেন। ডাক্তারের এমন কথার পর রোগীর পরিবার দৌঁড়ায় ক্লিনিক বা প্রাইভেট হাসপাতালে।
জীবন যেখানে রক্ষার স্থান, সেই হাসপাতাল অনেক ক্ষেত্রে হয়ে উঠছে মৃত্যুফাঁদ। চিকিৎসা নেওয়ার উদ্দেশ্যে মানুষ যায় আশায়, ফেরে হতাশায়। কারও ভাগ্যে থাকে ভুল চিকিৎসা, কারও জীবনের সমাপ্তি। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের এমন চিত্র দেশের সর্বত্র। আজ এমন এক সংকটে দেশের স্বাস্থ্য খাত। সংশ্লিষ্ট দপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন ও রাজনৈতিক আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে চলছে দেশের সর্বত্র
মফস্বল শহর থেকে রাজধানী সর্বত্র এমন অবস্থা। উপজেলা থেকে জেলা, এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার। বেশির ভাগই গড়ে উঠেছে লাইসেন্সবিহীন বা নিম্নমানের যন্ত্রপাতি নিয়ে, যেখানে স্বাস্থ্যবিধি ও চিকিৎসা মানে নামকাওয়াস্তে আনুগত্যও নেই।
প্রশ্ন জাগে, কাদের অনুমতিতে বা প্রশ্রয়ে এমন ব্যবসা চলছে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলো কারা পরিচালনা করছে, কাদের সিন্ডকেটে হরহামাশায়ই মানুষের পকেট কাটছে। জীবনের সবচেয়ে অসহায় সময়ে গুরুত্বপূর্ণ রোগীর জীবনের দায়ভার কার? ক্লিনিক বা হাসপাতাল সিন্ডিকেটে জড়িত অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি কেউ রাজনীতিতে, কেউ প্রশাসনে। তাই অভিযান চালালেও স্থায়ী সমাধান আসে না।
হাসপাতাল তো নয়, যেন ব্যবসাকেন্দ্র
রাজধানীসহ দেশের প্রায় প্রতিটি শহর, উপজেলা, এমনকি পাড়া-মহল্লায়ও দেখা যায় ডায়াগনস্টিক সেন্টার, হাসপাতাল বা চেম্বার কমপ্লেক্স। ছোট্ট একটি ভবন, কয়েকটি টেস্ট মেশিন, দুই-একজন নার্স আর একটি ডাক্তার বোর্ড এভাবেই শুরু হয় ‘হাসপাতাল ব্যবসা’। ব্যবসাটি অতিব লাভজনক হওয়ায় সরকারী হাসপাতলের পরিচিত এক/দুইজন ডাক্তারকে টার্গেট করে স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী মিলে বাহারী নামে খুলে দেন ক্লিনিক বা হাসপাতাল। শুরু হয় সাধারণ মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগে অমানবিক এই ব্যবসাটি।
দেখতে পাবেন লেখা থাকে হেলথ কেয়ার স্পেশালিস্ট হাসপাতাল, মডার্ন ডায়াগনস্টিক ,গ্লোবাল ক্লিনিক। নাম শুনে মনে হয় আন্তর্জাতিক মানের। কিন্তু ভিতরে গেলে বোঝা যায় বাস্তবতা উল্টো। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে নেই নিবন্ধিত ডাক্তার, নেই অ্যানেস্থেসিয়া বিশেষজ্ঞ, নেই সঠিক লাইসেন্স। এমনকি লাইফ সাপোর্ট বা আইসিইউ ইউনিটের নামে থাকে ভাঙা যন্ত্রপাতি, অকেজো অক্সিজেন সিলিন্ডার, অনভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান।
মূলত এসব ক্লিনিক বা হাসপাতালে চিকিৎসা নয়, চলে টেস্টের বাণিজ্য। রোগী এলেই ডাক্তারকে দিয়ে আগে একগাদা টেস্ট ধরিয়ে দেন।রক্ত, ইউরিন, ইসিজি, এক্স-রে, আলট্রাসনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান যা দরকার, যা দরকার নয়, সব করতেই হবে। যেন রোগী নয়, টেস্ট করানোই মূল লক্ষ্য।
ক্লিনিক ব্যবসার অদৃশ্য সিন্ডিকেট
এসব ক্লিনিক বা হাসপাতাল বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো একক কোন ব্যবসা নয়। র পিছনে থাকে বিশাল এক নেটওয়ার্ক। অনেক ডাক্তার নিজেরা সরাসরি জড়িত এসব প্রতিষ্ঠানে। তারা দিনের বেলায় সরকারি হাসপাতালে দায়িত্ব পালন করেন, রাতে বসেন বে-সরকারি ক্লিনিকে। অনেক সময় রোগীকে সরকারি হাসপাতাল থেকে বলে দেওয়া হয় এই টেস্টটা বাইরে থেকে করিয়ে আনুন। আর বাইরে বলতে বোঝানো হয় নিজেদের চেনা বা সংশ্লিষ্ট ক্লিনিক।
প্রতিটি টেস্টের জন্য ক্লিনিক মালিক ও সংশ্লিষ্ট ডাক্তারদের মধ্যে থাকে কমিশন চুক্তি। একজন রোগীর খরচ যত বাড়ে, ডাক্তারের ততই বাড়ে কমিশন। এসব ডাক্তারা কৌশল যেনে নেন রোগী কি করেন বা পরিবারের কে কি করেন। অবস্থাশালী হলেতো টেস্টের আইটেমও বাড়ে। ফলে যেখানে একটি রক্তপরীক্ষাই যথেষ্ট, সেখানে দেওয়া হয় দশটি টেস্টের পরামর্শ। অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা বলেন, বাংলাদেশে এখন চিকিৎসা নয়, টেস্টই চিকিৎসা।
লাইসেন্স আছে, তবু নিরাপত্তা নেই
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দেশে প্রায় ১৮ হাজার বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার আছে। এর মধ্যে প্রায় ৫ হাজার প্রতিষ্ঠান লাইসেন্সবিহীন বা মেয়াদোত্তীর্ণ লাইসেন্সে চলছে। অভিযান চলে, তালিকা প্রকাশ হয়, কয়েকদিন বন্ধ থাকে তারপর আবার খুলে যায় নতুন নামে।
এমনকি লাইসেন্সধারী হাসপাতালেও চিকিৎসা নিরাপত্তা নেই। অনেক হাসপাতালে নেই পর্যাপ্ত ডাক্তার, প্রশিক্ষিত নার্স বা আইসিইউ-টেকনিশিয়ান। অনেকে সরকারের স্বাস্থ্যবিধি বা ফায়ার সেফটি নিয়মও মানে না। ঢাকা শহরে একাধিক হাসপাতাল এখনো ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে চলছে, যেখানে আগুন লাগলে প্রাণরক্ষা অসম্ভব।
ভুল চিকিৎসা: আইনের চোখে ‘ভুল’, কিন্তু কারও কি দায় নেই?
রোগীর মৃত্যু হলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলে, ডাক্তার দায়ী। ডাক্তার বলেন, আমি তো প্রাইভেট কনসালট্যান্ট। আর প্রশাসন বলে, তদন্ত চলছে। ফলাফল হয়, কেউ দায় নেয় না, কেউ শাস্তি পায় না।
দেশে এখনো, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস আইন, কার্যকর হয়নি। ফলে চিকিৎসা বাণিজ্যের এই দৌরাত্ম্য ঠেকানোর কার্যকর উপায় নেই। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) অভিযোগ পেলে পদক্ষেপ নেয় বটে, কিন্তু প্রমাণের জটিলতায় বেশির ভাগ মামলা বছরের পর বছর ঝুলে থাকে।
সরকারের নজরদারি কোথায়?
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিটি করপোরেশন ও জেলা-উপজেলা প্রশাসন, তিনটি সংস্থা যৌথভাবে এই হাসপাতাল, ক্লিনিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে। কিন্তু সমন্বয়ের অভাবে কার্যকর তদারকি নেই। কোনো এলাকায় অভিযান চালানো হলেও তার আগে খবর ফাঁস হয়ে যায়। অনেক প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক আশ্রয়ে রক্ষা পায়। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, স্বাস্থ্য খাতে এখন লাভের লড়াই চলছে, যেখানে রোগীর জীবন গৌণ। যেখানে রোগী হচ্ছে ভোক্তা, চিকিৎসা একটি পণ্য।
কেন ব্যাঙের ছাতার মতো হাসপাতাল গড়ে উঠছে?
বিশ্লেষকরা বলেন, এর পেছনে আছে তিনটি বড় কারণ:
প্রথমত : এটি লাভজনক ব্যবসা। চিকিৎসা খাতে বিনিয়োগের মুনাফা দ্রুত পাওয়া যায়। এক্স-রে, ব্লাড টেস্ট, সিটি স্ক্যান সবকিছুতেই খরচ কম, আয় বেশি।
দ্বিতীয়ত : নিয়ন্ত্রণহীন প্রশাসন: লাইসেন্স ও অনুমোদনের জটিলতা থাকলেও অনেক সময় যোগাযোগ,বা ঘুষ দিয়েই তা পেয়ে যায় উদ্যোক্তারা।
তৃতীয়ত : জনগণের অসহায়ত্ব। সরকারি হাসপাতালে ভিড়, অব্যবস্থাপনা ও অবহেলার কারণে মানুষ বেসরকারি হাসপাতালে ছুটে যায়। আর সেই সুযোগেই ব্যবসায়ীরা মুনাফা তোলে।
ডাক্তারদের ভূমিকা ও দায়
সব ডাক্তার নয়, কিন্তু কিছু সংখ্যক চিকিৎসক এই অব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। অনেকেই ভিজিট শেয়ারিং নামের চুক্তিতে নির্দিষ্ট ক্লিনিকের সঙ্গে কাজ করেন। রোগী পাঠানোর বিপরীতে তাঁরা পান নির্দিষ্ট কমিশন। আর এর ফলে চিকিৎসা হয়ে পড়ে বাণিজ্যিক সিদ্ধান্তের অংশ। অন্যদিকে, যারা সততা বজায় রাখেন, তারা এই প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেন না।
সাধারণ মানুষের প্রতারণা ও অসহায়তা
গ্রামের মানুষ শহরে আসে ভালো চিকিৎসার আশায়। কিন্তু ঢুকে পড়ে প্রতারণার জালে। অভিভাবকরা বাচ্চার সর্দি নিয়ে আসে, আর ফিরে যায় হাতে একগাদা টেস্টের রিপোর্ট। বৃদ্ধ রোগীকে বলে দেওয়া হয়, অপারেশন লাগবে, যা হয়তো মোটেও প্রয়োজন নেই। আর রোগীর মৃত্যু হলে বলা হয়, আল্লাহর ইচ্ছা। কিন্তু এই কথার আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় হাসপাতালের অব্যবস্থা, ভুল চিকিৎসা, কিংবা মানবিক দায়িত্বহীনত।
সমাধান কি আছে:
স্বাস্থ্যসেবার এই দুরবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কিছু জরুরি পদক্ষেপ প্রয়োজন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের। লাইসেন্স নবায়ন ও কঠোর যাচাই: প্রত্যেক ক্লিনিক ও হাসপাতালের লাইসেন্স নবায়নের সময় মান যাচাই বাধ্যতামূলক করতে হবে। ভুল চিকিৎসা প্রতিরোধে বিশেষ আইন: মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস প্রতিরোধে কার্যকর আইন ও দ্রুতবিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন প্রয়োজন।
সরকারী হাসপাতালের ডাক্তারদের প্রাইভেট চিকিৎসা বন্ধ করে আইন করা। তবে নির্ধারিত ডিউটি টাইমের পরে কর্তব্যরত হাসপাতালে সরকারের নির্ধারিত অর্থে চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ দেয়া। ডাক্তারের কমিশন সংস্কৃতি আইন করে বন্ধ করে দেয়া। কমিশনভিত্তিক টেস্ট রেফারেল অবৈধ ঘোষণা করা।
সরকারি হাসপাতালের উন্নয়ন: সরকারি হাসপাতালগুলোতে সেবা ও আস্থা বাড়লে মানুষ বেসরকারি ফাঁদে পড়বে না।
স্বাস্থ্যসেবা পর্যবেক্ষণ বোর্ড: স্বাধীনভাবে কাজ করবে এমন একটি তদারকি বোর্ড, যেখানে থাকবে প্রশাসন, চিকিৎসক ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি।
চিকিৎসা কোনো পণ্য নয়: এটি মানবিক অধিকার। আজ সেই অধিকার পরিণত হয়েছে বাণিজ্যে। রোগীর কষ্টে, মৃত্যুর আতঙ্কে, ব্যবসায়ীদের লোভের হাসি শোনা যাচ্ছে।
বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার মূল ভিত্তি ভেঙে পড়ছে, কারণ আমরা চিকিৎসাকে মুনাফায় পরিণত করেছি। হাসপাতাল এখন আর আশ্রয় নয়, ভয়ের জায়গা। এই দায় নেবে কে? সরকার, ডাক্তার, নাকি আমরা সবাই, যারা চুপচাপ দেখি মানুষের জীবন শেষ হতে একটি ক্লিনিকের ভুল প্রেসক্রিপশনে?এখন সময়ের দাবি হচ্ছে এই নীরবতা ভাঙা। স্বাস্থ্যসেবায় ফিরিয়ে আনতে হবে মানবিকতা, নীতি ও আস্থা। নচেৎ হাসপাতালগুলো হয়তো চলবে, কিন্তু চিকিৎসা চলে যাবে মৃত্যুর ঘরে।